অবশিল্পায়ন অথবা De-industrialization বলতে আমরা কি বুঝি, সেই সম্পর্কে চারটি ধারণা প্রচলিত আছে-
অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপীয় শক্তিগুলি এশিয়ার দেশগুলির উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা অথবা এশিয়ার দেশগুলোকে উপনিবেশে পরিণত করার ফলে এই সমস্ত দেশগুলির দ্রব্য উৎপাদনের অবক্ষয় দেখা দেয় এবং এই সমস্ত দেশগুলির "G D P" হ্রাস পায়| এই দেশগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল ভারত, চীন এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ|
আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে ভারত যথার্থ অর্থে একটি শিল্পোন্নত দেশ নয়, তবে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর বিচারে বিশেষ করে ভারতবর্ষে ইউরোপীয় শক্তির আগমনের পূর্বে ভারত ছিল বিশ্বের একটা গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক ক্ষেত্র| ভারতের চিরাচরিত গ্রামীণ অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য ছিল হস্তশিল্প এবং কৃষিকার্যের মিশ্রন, কিন্তু ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতির অভ্যন্তরীণ ভারসাম্য ব্রিটিশ শাসনকালে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়|
ভারতের চিরাচরিত হস্তশিল্প ধীরে ধীরে তার মর্যাদা এবং গুরুত্ব হারায় ও অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে কার্যত অবক্ষয়ের দিকে এগিয়ে যায় এবং উনবিংশ শতকের শুরু থেকে এই অবক্ষয়ের গতি দ্রুত বৃদ্ধি পায়|
- উৎপাদনের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি অবক্ষয় অথবা উৎপাদন ক্ষেত্রে নিয়োগের পরিমাণ হ্রাস|
- উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে সেবামূলক ক্ষেত্রে সঞ্চালন, যার ফলে উৎপাদন ক্ষেত্রে নিয়োগের অংশ হ্রাস পায়|
- উৎপাদন ক্ষেত্রে উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী অংশ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অবক্ষয় হয়, এর ফলস্বরূপ যথাপোযুক্ত উদ্বৃত্তের রপ্তানি এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আমদানি অর্থনীতিতে ভারসাম্য বজায় রাখতে অক্ষম|
- বাণিজ্য ভারসাম্যের ক্ষেত্রে এর ফলস্বরূপ কোন দেশ বা কোন অঞ্চল তার প্রয়োজনীয় আমদানি বজায় রাখতে অক্ষম হয়, অর্থাৎ তার প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আমদানির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বিনিয়োগ করতে ব্যর্থ হয়| এর ফল হিসেবে অর্থনীতি বিশেষভাবে অবক্ষয়ের দিকে ধাবিত হয়|
অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপীয় শক্তিগুলি এশিয়ার দেশগুলির উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা অথবা এশিয়ার দেশগুলোকে উপনিবেশে পরিণত করার ফলে এই সমস্ত দেশগুলির দ্রব্য উৎপাদনের অবক্ষয় দেখা দেয় এবং এই সমস্ত দেশগুলির "G D P" হ্রাস পায়| এই দেশগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল ভারত, চীন এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ|
 |
| বর্তমানে ভারতের মানচিত্র |
 |
| ইউরোপীয় মানচিত্র |
আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে ভারত যথার্থ অর্থে একটি শিল্পোন্নত দেশ নয়, তবে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর বিচারে বিশেষ করে ভারতবর্ষে ইউরোপীয় শক্তির আগমনের পূর্বে ভারত ছিল বিশ্বের একটা গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক ক্ষেত্র| ভারতের চিরাচরিত গ্রামীণ অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য ছিল হস্তশিল্প এবং কৃষিকার্যের মিশ্রন, কিন্তু ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতির অভ্যন্তরীণ ভারসাম্য ব্রিটিশ শাসনকালে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়|
ভারতের চিরাচরিত হস্তশিল্প ধীরে ধীরে তার মর্যাদা এবং গুরুত্ব হারায় ও অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে কার্যত অবক্ষয়ের দিকে এগিয়ে যায় এবং উনবিংশ শতকের শুরু থেকে এই অবক্ষয়ের গতি দ্রুত বৃদ্ধি পায়|
অবশিল্পায়ন বলতে বোঝায় শিল্পায়নের অবস্থাকে| 1940 খ্রিস্টাব্দ নাগাদ "অবশিল্পায়ন" শব্দটির প্রথম ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়| এই শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো, দেশের শিল্পগত ক্ষমতার অবক্ষয় বা ধ্বংস|
Paul Bairoch বিশ্বের উৎপাদিত দ্রব্যের হারকে হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, বিশ্বের বাজারে ভারতের উৎপাদিত দ্রব্যের অংশ ছিল যথেষ্ট উপরে| 1800 খ্রিস্টাব্দে এর পরিমান ছিল 9.7 per cent, 1860 খ্রিস্টাব্দে নাগাদ এর পরিমাণ দাঁড়ায় 8.6 per cent এবং 1913 খ্রিস্টাব্দে এর পরিমান হয় 1.4 per cent, সুতরাং বিশ্ববাজারে ভারতীয় উৎপাদিত দ্রব্যের হ্রাস ছিল প্রকৃতপক্ষে অবশিল্পায়নের অথবা ভারতীয় দ্রব্য উৎপাদনের অবক্ষয়ের দৃষ্টান্তস্বরূপ|
ড্যানিয়েল র্থনার অবশিল্পায়ন বলতে বুঝিয়েছেন, সমগ্র কর্ম নিয়োগের বিচারে শিল্পক্ষেত্রে কর্ম নিয়োগের পরিমান হ্রাসকে অথবা শিল্প ক্ষেত্রে নির্ভরশীল জনসংখ্যার পরিমাণ হ্রাসকে| যদিও ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এই নিয়মের ঠিক বিপরীত অবস্থা লক্ষ্য করা গিয়েছিল| পশ্চিমী দেশগুলির ক্ষেত্রে দেখা যায়, শিল্পায়নের প্রাথমিক ক্ষেত্রে অর্থাৎ কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত মানুষের সংখ্যা হ্রাস এবং শিল্পক্ষেত্রে নিযুক্ত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি, কিন্তু ভারতে হস্তশিল্প তবে আগমনের পূর্বে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল|
যদিও অবশিল্পায়নের এই শব্দটি জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা যায় যে, বিংশ শতকে স্বদেশী আন্দোলনের ক্ষেত্রে এর একটি রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল এবং প্রকৃত পক্ষে অবশিল্পায়ন ঘটেছিল, কিন্তু বিদেশী অর্থনীতিবিদদের বিশেষ করে মরিচ ডি মরিস, ড্যানিয়েল র্থনার এবং অ্যালিস র্থনার যুক্তি দিয়ে বলেছেন যে, ভারতের অবশিল্পায়নের ধারণা একটি অলীক ঘটনা| এর কোন বাস্তব ভিত্তি নেই|
Paul Bairoch বিশ্বের উৎপাদিত দ্রব্যের হারকে হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, বিশ্বের বাজারে ভারতের উৎপাদিত দ্রব্যের অংশ ছিল যথেষ্ট উপরে| 1800 খ্রিস্টাব্দে এর পরিমান ছিল 9.7 per cent, 1860 খ্রিস্টাব্দে নাগাদ এর পরিমাণ দাঁড়ায় 8.6 per cent এবং 1913 খ্রিস্টাব্দে এর পরিমান হয় 1.4 per cent, সুতরাং বিশ্ববাজারে ভারতীয় উৎপাদিত দ্রব্যের হ্রাস ছিল প্রকৃতপক্ষে অবশিল্পায়নের অথবা ভারতীয় দ্রব্য উৎপাদনের অবক্ষয়ের দৃষ্টান্তস্বরূপ|
 |
| কৃষক |
 |
| কৃষি জমি |
ড্যানিয়েল র্থনার অবশিল্পায়ন বলতে বুঝিয়েছেন, সমগ্র কর্ম নিয়োগের বিচারে শিল্পক্ষেত্রে কর্ম নিয়োগের পরিমান হ্রাসকে অথবা শিল্প ক্ষেত্রে নির্ভরশীল জনসংখ্যার পরিমাণ হ্রাসকে| যদিও ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এই নিয়মের ঠিক বিপরীত অবস্থা লক্ষ্য করা গিয়েছিল| পশ্চিমী দেশগুলির ক্ষেত্রে দেখা যায়, শিল্পায়নের প্রাথমিক ক্ষেত্রে অর্থাৎ কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত মানুষের সংখ্যা হ্রাস এবং শিল্পক্ষেত্রে নিযুক্ত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি, কিন্তু ভারতে হস্তশিল্প তবে আগমনের পূর্বে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল|
যদিও অবশিল্পায়নের এই শব্দটি জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা যায় যে, বিংশ শতকে স্বদেশী আন্দোলনের ক্ষেত্রে এর একটি রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল এবং প্রকৃত পক্ষে অবশিল্পায়ন ঘটেছিল, কিন্তু বিদেশী অর্থনীতিবিদদের বিশেষ করে মরিচ ডি মরিস, ড্যানিয়েল র্থনার এবং অ্যালিস র্থনার যুক্তি দিয়ে বলেছেন যে, ভারতের অবশিল্পায়নের ধারণা একটি অলীক ঘটনা| এর কোন বাস্তব ভিত্তি নেই|
অবশিল্পায়নের কারণ
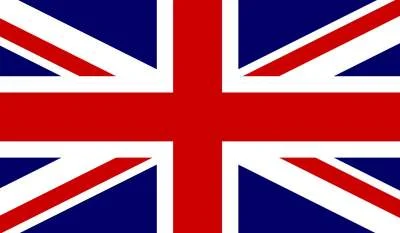 |
| ব্রিটিশ পতাকা |
ভারতবর্ষে শিল্প বলতে সুতি বস্ত্র শিল্পকে মূলত বোঝায় এবং অবশিল্পায়ন বলতে সুতিবস্ত্র শিল্পের অবক্ষয়কে বোঝায়| ভারতে সুতিবস্ত্র শিল্প ছিল কৃষি ক্ষেত্রের পরে সবথেকে বেশি কর্ম নিয়োগের ক্ষেত্র| 1800 খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ভারতের সুতিবস্ত্র ছিল পৃথিবীর বিখ্যাত, কিন্তু শিল্পের অবক্ষয় শুরু হয় ব্রিটিশ শাসনকাল থেকে| এর কারণগুলি হল-
- ভারতবর্ষে সুতিবস্ত্র শিল্পে বিরাট আঘাত আসে ইংল্যান্ডের যন্ত্র নির্মিত বস্ত্রের দ্বারা| বিশেষ করে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের পর ভারতবর্ষে ব্রিটিশ পণ্যের আমদানির পরিমাণ বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, এরফলে ভারতের বাজার ইংল্যান্ড জাত বস্ত্রে ছেয়ে যায়| এরফলে ভারতবর্ষে ব্যাপক পরিমাণে বেকারত্বের সূচনা হয় এবং কল্পনাতীত ভাবে ভারতীয় হস্তশিল্পী এবং বুননকারীদের আয় হ্রাস পায় এবং এর পাশাপাশি অন্যান্য যে সমস্ত শিল্পের উপরে প্রভাব পড়েছিল সেগুলি হল- রেশম শিল্প, কাঁচ শিল্প প্রভৃতি|
- ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব ঘটেছিল অষ্টাদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে নাগাদ| ভারতবর্ষে অবশিল্পায়নের প্রকৃত সূত্রপাত ঘটেছিল সুতিবস্ত্র শিল্পের ধীরে ধীরে অবক্ষয়ের ফলে| ভারত বিদেশে সুতিবস্ত্র শিল্পে রপ্তানিকারক দেশ থেকে আমদানিকারক দেশে পরিণত হয়েছিল| এর ফলে ভারতের চিরাচরিত হস্তশিল্পের "গ্রহন" লেগে যায়| এর পিছনে কতগুলি কারণ ছিল, অর্থনীতিবিদ গ্যাডগিল এর তিনটি কারণকে চিহ্নিত করেছেন- 1.মুঘল শাসন কালে রাজসভার সংস্কৃতির অবসান এবং অভিজাততন্ত্রের অবক্ষয়| 2.বহু বিদেশী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের আগমন এবং তাদের প্রথা| 3.যন্ত্রে উৎপাদিত দ্রব্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা|
রাজসভার সংস্কৃতির অবসান
 |
সুতি বস্ত্র |
ভারতীয় সুতি বস্ত্র শিল্পের মুখ্য ক্রেতা ছিল ভারতের বিভিন্ন রাজপরিবারগুলি এবং শহরের অভিজাতরা, কিন্তু ব্রিটিশ শাসনকালে এই রাজপরিবারগুলি ধ্বংস হওয়ায় ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের অভ্যন্তরীণ বাজার নষ্ট হয়ে যায়|
যাইহোক কোন কোন ক্ষেত্রে অভিজাত এবং শহরের ধনী ব্যক্তিরা ভারতীয় সুতিবস্ত্র শিল্পের বড় ধরনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, কিন্তু ধীরে ধীরে সমগ্র ভারত জুড়ে ব্রিটিশ শাসনের ক্রমবিস্তার এবং ভারতীয় রাজ পরিবারগুলির অবসান হেতু ভারতীয় হস্তশিল্পীরা তাদের হস্তশিল্পের কারখানাগুলিকে বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন| এই প্রসঙ্গে বলা যায়, ভারতের সুতিবস্ত্র শিল্পকে সাহায্য করার মতো আর কোন বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না|
.......................................
যাইহোক কোন কোন ক্ষেত্রে অভিজাত এবং শহরের ধনী ব্যক্তিরা ভারতীয় সুতিবস্ত্র শিল্পের বড় ধরনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, কিন্তু ধীরে ধীরে সমগ্র ভারত জুড়ে ব্রিটিশ শাসনের ক্রমবিস্তার এবং ভারতীয় রাজ পরিবারগুলির অবসান হেতু ভারতীয় হস্তশিল্পীরা তাদের হস্তশিল্পের কারখানাগুলিকে বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন| এই প্রসঙ্গে বলা যায়, ভারতের সুতিবস্ত্র শিল্পকে সাহায্য করার মতো আর কোন বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না|
বিদেশি শাসন এবং তার প্রভাব
ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠা ভারতীয় হস্তশিল্পের উপরে গভীর প্রভাব ফেলেছিল প্রত্যক্ষভাবে এবং পরোক্ষভাবে| ব্রিটিশ শিল্পের প্রয়োজনে একটা নতুন শ্রেণী সৃষ্টি করা হয়েছিল| এই শ্রেণীর মধ্যে ছিল ইউরোপীয় কর্মচারীবৃন্দ, ভ্রমণকারী এবং ভারতীয় বাবু সমাজ ও কালো ভারতীয় সাহেবগণ| এই ইউরোপীয় কর্মচারীবৃন্দ ব্রিটিশজাত দ্রব্যের ব্যবহার এবং আমদানির পক্ষপাতী ছিল| এর ফলস্বরূপ ভারতীয় বস্ত্রশিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যায়|
যন্ত্রে উৎপাদিত দ্রব্যের সঙ্গে প্রতিযোগীতা
1813 খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির একচেটিয়া কারবারের অবসান হয়| ফলে ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের প্রভাব ভারতে এসে পড়ে| ইংল্যান্ডের দ্রব্য যাতে অবাধে ভারতে আসতে পারে তার জন্য আমদানি শুল্ক কমিয়ে দেওয়া হয়| কিভাবে ইংল্যান্ডে কারখানার তৈরি কাপড় বাংলার বাজারে দখল করে নেই একটা পরিসংখ্যান থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায়|
1813-14 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইংল্যান্ড থেকে বাংলায় 91,800 টাকার কাপড় আমদানি করা হয়েছিল| 1822-23 খ্রিস্টাব্দে আমদানির পরিমাণ বেড়ে হয় 67,77,279 টাকা| 1829-30 খ্রিস্টাব্দে পর থেকে আমদানির পরিমাণ আরও বাড়তে থাকে|
একই সাথে বাংলা থেকে ইংল্যান্ডে রপ্তানির পরিমাণ কমতে থাকে| 1813-14 খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে 34,29,043 টাকার মূল্যে সুতিবস্ত্র রপ্তানি করা হয়েছিল| 1828-29 খ্রিস্টাব্দে এর পরিমাণ কমে দাঁড়ায় 1,64,408 টাকা| অর্থাৎ সস্তা দরে বিদেশি কাপড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে ভারতীয় তাঁতিরা পিছু হটতে আরম্ভ করে|
1813-14 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইংল্যান্ড থেকে বাংলায় 91,800 টাকার কাপড় আমদানি করা হয়েছিল| 1822-23 খ্রিস্টাব্দে আমদানির পরিমাণ বেড়ে হয় 67,77,279 টাকা| 1829-30 খ্রিস্টাব্দে পর থেকে আমদানির পরিমাণ আরও বাড়তে থাকে|
একই সাথে বাংলা থেকে ইংল্যান্ডে রপ্তানির পরিমাণ কমতে থাকে| 1813-14 খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে 34,29,043 টাকার মূল্যে সুতিবস্ত্র রপ্তানি করা হয়েছিল| 1828-29 খ্রিস্টাব্দে এর পরিমাণ কমে দাঁড়ায় 1,64,408 টাকা| অর্থাৎ সস্তা দরে বিদেশি কাপড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে ভারতীয় তাঁতিরা পিছু হটতে আরম্ভ করে|
অবশিল্পায়নের ফলাফল
ভারতীয় শিল্পের ধ্বংসের ফল ছিল সুদূর প্রসারী ও গভীর| যথা-
- সুতিবস্ত্র শিল্পের ধ্বংসের ফলে ভারতে সূক্ষ্ম শিল্পের ঐতিহ্য চিরতরে নষ্ট হয়ে যায়| এই সমস্ত শিল্পের সঙ্গে যুক্ত শহরের কারিগর ও শিল্পীরা তাদের চিরাচরিত পেশা পরিত্যাগ করে কর্মের সন্ধানে অনত্র চলে যেতে বাধ্য হয়| এই কারণে শহরগুলি ক্রমশ জনশূন্য হয়ে পড়ে| মসলিন বস্ত্র শিল্পের প্রধান কেন্দ্র ঢাকাতে এর অবস্থান হয়েছিল| অন্যদিকে গ্রামগুলিতে ভিড় ক্রমশ বাড়তে থাকে|
- যে সমস্ত তাঁতী তাদের চিরাচরিত পেশা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়, তারা চাষের কাজ গ্রহণ করে, ফলে কৃষির উপর চাপ বাড়ে| বস্তুত বস্ত্র শিল্প ধ্বংসের ফলে বহু লোক বেকার হয়ে যায়| সুতো কাটার কাজে যেসব মহিলারা কর্মচারী হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন তারা পুরোপুরি বেকার হয়ে পড়ে| তাদের পক্ষে কৃষি বা অন্য কোন জীবিকা গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না| বস্ত্রবয়ন শিল্পে নিযুক্ত দশ লক্ষের বেশি মানুষ বেকার হয়ে পড়ে| তাই এক কথায় বলা যায়, বস্ত্রশিল্পের ধ্বংসের ফলে চাষীদের সীমাহীন দারিদ্র্যের মধ্যে পড়তে হয়|
- রমেশচন্দ্র দত্ত, ড. রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মতে, উনবিংশ শতকের গোড়ায় বাংলায় বস্ত্রশিল্পের ধ্বংস বাংলার অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে দেয়| তবে বস্ত্রশিল্পের ধ্বংসের ধ্বংসের ক্ষতি কিছুটা পূরণ হয়েছিল কাঁচা রেশম, চিনি এবং নীল চাষে প্রসারের ফলে| কাঁচামালের উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধি পায়|
- ভারতে দারিদ্রতা বৃদ্ধি পায়| লোকের কৃষি ছাড়া অন্য কোন জীবিকা না থাকায় এবং শিল্প ও ব্যবসা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ভারতবর্ষে দুর্দশা দেখা দেয়|
তথ্যসূত্র
- সুমিত সরকার, "আধুনিক ভারত"
- শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, "পলাশি থেকে পার্টিশন"
- Ishita Banerjee-Dube, "A History of Modern India".
সম্পর্কিত বিষয়
- অবশিল্পায়ন বিতর্ক (আরো পড়ুন)
- অবশিল্পায়ন কাকে বলে (আরো পড়ুন)
- সম্পদের বহির্গমন তত্ত্ব এবং এটি কিভাবে বাংলার অর্থনীতিকে প্রভাবিত করেছিল (আরো পড়ুন)
- ১৮৫৮ সালের ভারত শাসন আইন (আরো পড়ুন)
সম্পূর্ণ পোস্টটি পড়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ| আশাকরি আমাদের এই পোস্টটি আপনার ভালো লাগলো| আপনার যদি এই পোস্টটি সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন থাকে, তাহলে নিচে কমেন্টের মাধ্যমে আমাদেরকে জানাতে পারেন এবং অবশ্যই পোস্টটি শেয়ার করে অপরকে জানতে সাহায্য করুন|



